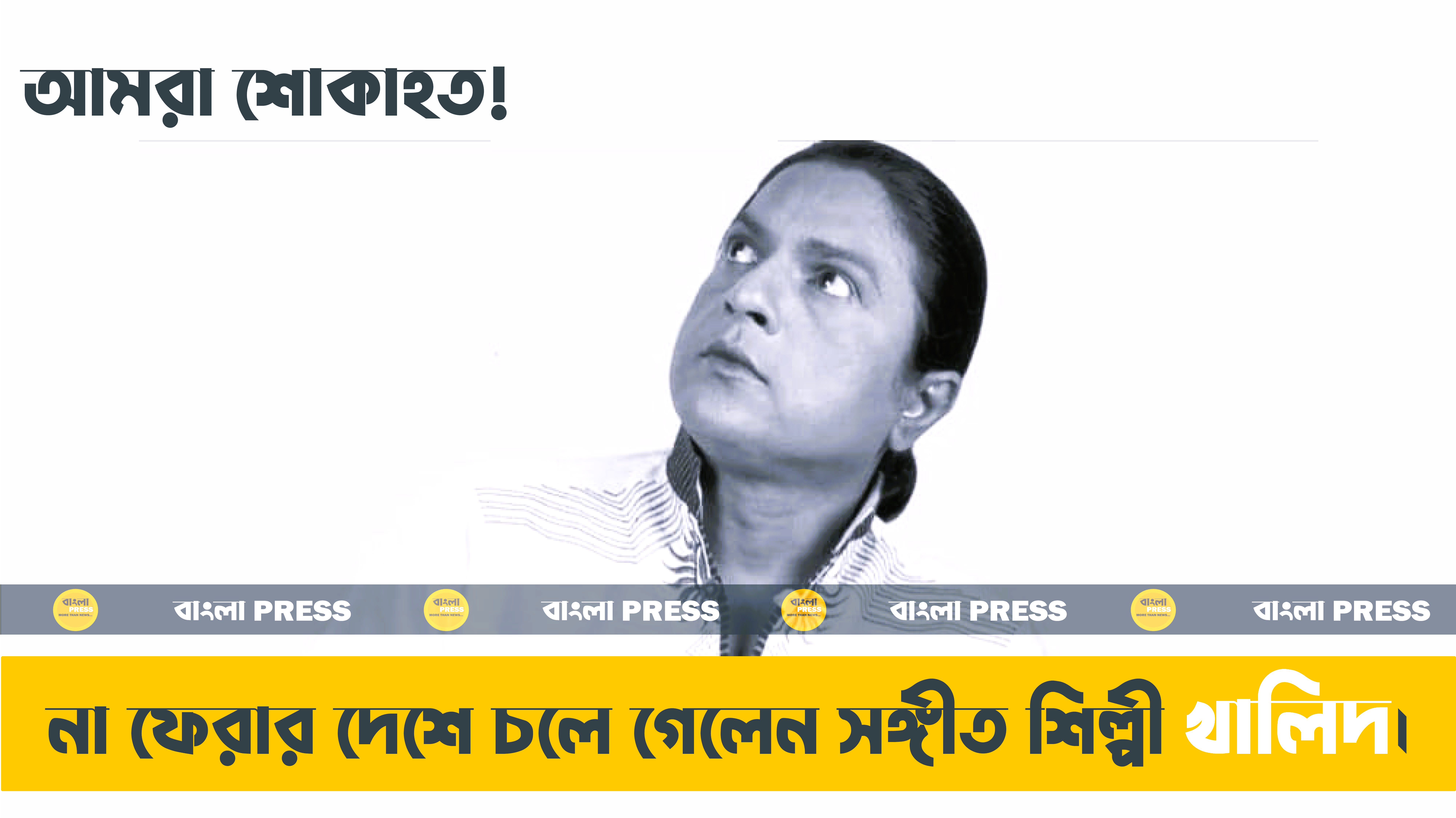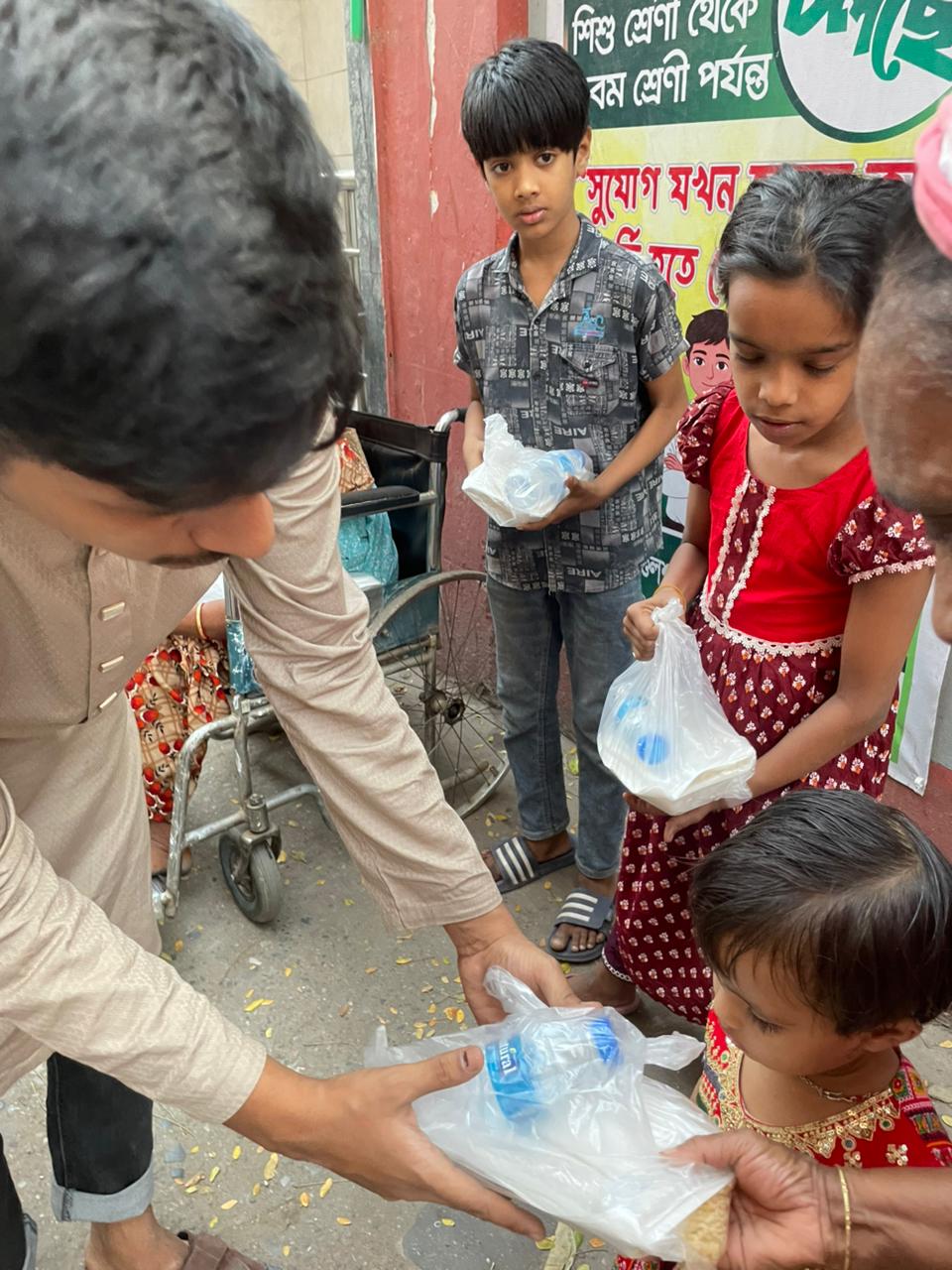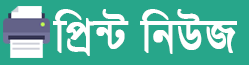
আর্যভট্ট ছিলেন ভারতীয় গণিত এবং ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার ধ্রুপদী যুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ, পদার্থবিদ এবং জ্যোতির্বিদ। আর্যভট্টকে গুপ্তযুগের নিউটন বলেও আখ্যায়িত করা হয়।
আর্যভট্টের জন্ম –
আর্যভট্টের জন্ম নিয়ে মতোবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেন তিনি পাটনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কুসুমপুরে। আবার কেউ বলেন এই মহাপুরুষের জন্ম অশ্মকা নামক জায়গায়, যা বর্তমানে মহারাষ্ট্র নামে পরিচিত। তবে জীবনের বেশিরভাগ সময়ে তিনি কুসুমপুরেই কাটান বলে জানা যায়। সেখানে তার পরিচিতি ছিল ভিন্ন নামে। তিনি সেখানে পরিচিত ছিলেন “আর্যভ” নামে। তবে তার জন্মসাল নিয়ে সেভাবে কোন তথ্য প্রমাণ মিলে নি। তারই একটি বইয়ে তিনি লিখেছেন, তিন যুগপদ ও ষটযুগ অস্তকালে তার বয়স ছিল ২৩ বছর। সেই লেখা থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র হিসেবে গণনা করলে দেখা যায়, তিনি জন্মেছিলেন ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে।
আর্যভট্টের উচ্চশিক্ষা –
কিছু তথ্যমতে জানা যায় যে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য কুসুমপুরায় গিয়েছিলেন। তার কাজের অধিকাংশই তিনি করেছিলেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানেই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন তিনি। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু ও বিজ্ঞ একজন মানুষ। শিক্ষাশেষে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। কেউ কেউ বলেছেন, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবেও আর্যভট্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।
আর্যভট্টের অবদান –
ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে আর্যভট্টের অবদান অনস্বীকার্য। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে আবর্তন করে এই সত্য তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। তার হাত ধরেই ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। তার কাজেই দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির পূর্ণ ব্যাবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। দশমিক পদ্ধতিকে ব্যবহার করে তিনিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন, এর মাঝে ছিল সংখ্যার বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয়। আধুনিক ত্রিকোণমিতির সূচনাও হয় তার হাত ধরেই। এমনিকি “কুত্তক” নামে তিনি একটি সাধারণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন যা দ্বারা একাধিক অজানা রাশি সম্বলিত সমীকরণ সমাধান করা যায়। তার দ্বিতীয় গ্রন্থে পাইয়ের মান ও ব্যাবহার সম্পর্কেও ধারণা পায় ভারতীয় গণিত।
আর্যভট্টের গ্রন্থ সমুহ –
আর্যভট্ট গ্রন্থ রচনা করেছেন পদবাচ্যের আকারে। তার রচনা ও গাণিতিক ধারণা ও প্রমাণ ছিল সাবলীল।
গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত আর্যভট্টের বিভিন্ন কাজ মূলত দুটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বলে জানা গেছে। এর মাঝে ‘আর্যভট্টীয়’ একটি অন্যতম পুস্তক, যেটি উদ্ধার করা গিয়েছে। এটি রচিত চার খণ্ডে, মোট ১১৮টি স্তোত্রে।
অন্য যে কাজটি সম্পর্কে জানা যায় সেটি হল ‘আর্য-সিদ্ধান্ত’। আর্য-সিদ্ধান্তের কোন পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যায়নি, তবে বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত এবং প্রথম ভাস্করের কাজে এটির উল্লেখ মেলে।
জ্যোতির্বিদ্যায় আর্যভট্টের অবদান –
আর্যভট্টের অবদান শুধু গণিতে নয়, জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত অনেক অবদান তিনি তার জীবদ্দশায় রেখে গেছেন।
তিনি পৃথিবীর আক্ষিক গতির হিসাব করেছিলেন। তার প্রমাণ অনুযায়ী পৃথিবীর পরিধি ছিল ৩৯,৯৬৮ কিলোমিটার, যেটা সে সময় পর্যন্ত বের করা যেকোন পরিমাপের চেয়ে শুদ্ধতর ছিল (ভুল মাত্র ০.২%)।
আর্যভট্টীয় বইটির গোলপাদ অংশে আর্যভট্ট উদাহরণের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন যে পৃথিবী নিজ অক্ষের সাপেক্ষে ঘোরে। তিনি বলে গিয়েছিলেন, সৌর জগতে গ্রহগুলোর কক্ষপথের আকৃতি উপবৃত্তাকৃতির। তিনি সৌরজগতের পৃথিবীকেন্দ্রিক নাকি সূর্যকেন্দ্রিক মডেল ব্যবহার করেছিলেন, যদিও সেটি নিয়ে সেই সময় বিতর্ক ছিল। B.L. van der Waerden, Hugh Thurston এর লেখায় আর্যভট্টের জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত হিসাব নিকাশের পদ্ধতিকে সরাসরি সূর্যকেন্দ্রিক বলে দাবি করা হয়েছে। Noel Swerdlow অবশ্য এ জন্য B.L. van der Waerden এর প্রত্যক্ষ সমালোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে আর্যভট্টের ধারণায় সৌরজগৎ পৃথিবীকেন্দ্রিকই ছিল। অপর দিকে Dennis Duke এর মতে, আর্যভট্টের কাজের পদ্ধতি সূর্যকেন্দ্রিক ছিল, তবে সেটি আর্যভট্ট লক্ষ করেননি কিংবা জানতেন না। আর্যভট্ট সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের হিন্দু পৌরাণিক ধারণার পরিবর্তে প্রকৃত কারণগুলো ব্যাখ্যা করে গেছেন। সেই সাথে তিনি সূর্য গ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণের সময়কাল নির্ণয়ের পদ্ধতিও বের করেছিলেন । আর্যভট্ট বলেছিলেন যে চাঁদের আলো আসলে সূর্যের আলোর প্রতিফলনেরই ফলাফল।


 বাংলাপ্রেস নিউজ ডেস্ক
বাংলাপ্রেস নিউজ ডেস্ক